কেমন ছিল একাত্তরের ঈদুল ফিতর?কেমন ছিল একাত্তরের ঈদুল ফিতর?
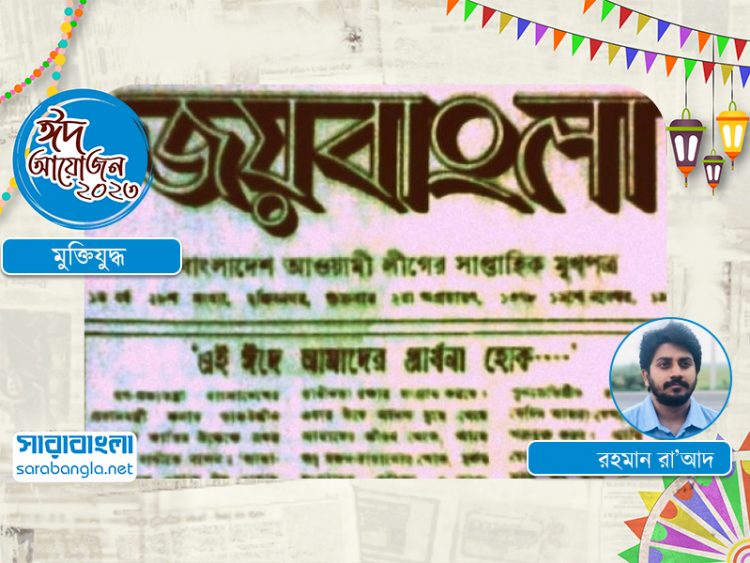
‘চাঁদ তুমি ফিরে যাও...
দেখো মানুষের খুনে খুনে রক্তিম বাংলা
রূপসী আঁচল কোথায় রাখবো বলো?’
একাত্তরের ২০ নভেম্বর ছিল পবিত্র ঈদুল ফিতর। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিশেষ অনুষ্ঠানমালার মধ্যে অন্যতম অসামান্য ছিল শহীদুল ইসলামের লেখা ও অজিত রায়ের সুরে এই গানটি। কোরাসে গেয়েছিলেন শিল্পী রুপা ফরহাদসহ আরো অনেকে। ঈদের আনন্দ ভাগ করে নিতে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা অপেক্ষায় থাকে সারাবছর, খুবই বিশেষ এই উপলক্ষ্যের গুরুত্ব বলাই বাহুল্য। কিন্তু একাত্তরের সেই শ্বাপদসংকুল সময়ে ঈদের আনন্দ উপভোগ বা ঈদ পালনের কথা কেউ চিন্তাও করেনি। অন্তহীন কষ্ট আর যন্ত্রণায় জর্জরিত সাধারণ মানুষ, দেশটা পরিণত হয়েছে এক বিশাল বধ্যভূমিতে, প্রতিমুহুর্তেই তাড়া করে ফিরছে মৃত্যু। অন্যদিকে শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে শত্রুমুক্ত ভূখন্ডে পরবর্তী ঈদ উদযাপন দৃঢ় সংকল্পে বলীয়ান মুক্তিযোদ্ধারা। এই সবই যেন শহীদুল তুলে আনলেন তার আবেগমথিত গানের কথায়।
গানটি এত তীব্রভাবে ভেতরটা নাড়িয়ে দিয়েছিল যে, শুধু মুক্তিযোদ্ধারাই নয়, সাধারণ মানুষ ঈদের দিন এই গান শুনে কেঁদে আকুল হয়ে বুক ভাসিয়েছে। ঈদের চাঁদকে ফিরে যেতে বলার মত অভাবিত বেদনাবিধুর বাস্তবতা একাত্তরের আগে কখনো শুধু বাঙালী মুসলমান নয়, পৃথিবীর অন্য কোন প্রান্তের মুসলমানদের নসীবে ঘটেছে বলে মনে হয় না।

২০ নভেম্বর কলকাতায় অস্থায়ী সরকারের ঈদের জামাত। সামনে সারিতে ঈদের নামাজরত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ, প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানী এবং অন্যান্য।
বিজ্ঞাপন
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে সংবাদ বিভাগের দায়িত্বে থাকা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী গানটির তৈরি ও প্রচারের ইতিহাস জানান তার স্মৃতিকথায়- “...ঈদের দুদিন আগেই গানটি রেকর্ড করলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। কিন্তু ঠিক হলো চাঁদ উঠলে এই গানটি প্রচারিত হবে। হলোও তাই। উঠল ঈদের চাঁদ আকাশে। স্বাধীন বাংলা বেতারে গেয়ে উঠল সমবেত কণ্ঠে, ‘চাঁদ তুমি ফিরে যাও, ফিরে যাও।’ ওরা (পাকিস্তানি) সেদিন অবরুদ্ধ বাংলার ভাই-বোন, মা ও বাবার মনেও স্বস্তি দেয়নি। ওদের ভয়ার্ত জীবনের একটাই চিন্তা ছিল- কি করে শত্রুর কবল থেকে এই দেশকে বাঁচাবো। আর ভাবছিলেন আমাদের কথা, যারা যুদ্ধে ছিলাম…” শহীদুল ইসলাম আজ কয়েকবছর হলো মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু তিনি সেদিনের এই ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করেছিলেন সকল মুক্তিযোদ্ধার হয়ে।
১৯৭১ সালের ঈদ ছিল এমনই। বিষণ্ণ, ধূসর হতাশার এক আখ্যান, চারদিকের লাশ আর পোড়ামাটির বীভৎসতা। যারা মারা গেছে, তারা সবকিছুর উর্ধ্বে। এক বিব্রতকর যন্ত্রণায় ছিল শহরে অবরুদ্ধ মানুষগুলো। জীবন ও পরিবারের জন্য ভয় আর উৎকণ্ঠার মধ্যেই তাদের ঈদ কেটেছে বিষাদময় হতাশায়। শিল্পী হাশেম খান ছিলেন আরামবাগে। তার ‘গুলিবিদ্ধ একাত্তর’ গ্রন্থে তিনি জানিয়েছেন, ঈদের জামাত শেষে পাকিস্তানের কল্যাণ কামনা ও হানাদার বাহিনীর জন্য মোনাজাতও হয়েছিল। যদিও হাশেম খানের দৃঢ় ধারণা, বন্দুকের মুখে ইমাম সাহেবকে বাধ্য হয়ে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনী ও রাজাকার আলবদরদের জন্য যে দোয়া করতে হল, সেই মেকি মোনাজাতে উপস্থিত মুসল্লিদেরও সামিল হবার ভয়ার্ত অভিনয় করতে হয়েছে। বর্বর গণহত্যাকারীদের জন্য মন থেকে কারো দোয়া চাইবার প্রশ্নই আসে না। বর্ণনায় তিনি লেখেন “...আজ ঈদ। আনন্দের দিন। উৎসবের দিন, আনন্দের দিন। কিন্তু কী আনন্দ করবো এবার আমরা? নতুন জামাকাপড় বা পোশাক কেনাকাটার আগ্রহ নেই! শিশু-কিশোরদের কোনো আবদার নেই। চাওয়া-পাওয়া নেই। বাড়িতে বাড়িতে কি পোলাও কোমরা ফিরনী রান্না হবে? আমার বাড়িতে তো এসবের কোনো আয়োজন হয়নি। প্রতিটি বাঙালির বাড়িতে এরকমই তো অবস্থা।
বিজ্ঞাপন ঈদের নামাজের পর বঙ্গবন্ধু পুত্র শেখ কামালের সঙ্গে কোলাকুলি করছেন তাজউদ্দীন আহমেদ
ঈদের নামাজের পর বঙ্গবন্ধু পুত্র শেখ কামালের সঙ্গে কোলাকুলি করছেন তাজউদ্দীন আহমেদ
 ঈদের নামাজের পর বঙ্গবন্ধু পুত্র শেখ কামালের সঙ্গে কোলাকুলি করছেন তাজউদ্দীন আহমেদ
ঈদের নামাজের পর বঙ্গবন্ধু পুত্র শেখ কামালের সঙ্গে কোলাকুলি করছেন তাজউদ্দীন আহমেদবিজ্ঞাপন
... তিনতলার বারান্দা থেকে আরামবাগের শুরু ও ফকিরাপুল বাজারের মাঝামাঝি অবস্থানে মসজিদটি দেখা যায়। সকাল ৮ থেকে মাইকে ঘোষণা দিচ্ছে সাড়ে ৯ টায় নামাজ হবে। যথাসময়ে মসজিদে গিয়ে হাজির হলাম। নামাজ হলো, খুৎবা হলো, মোনাজাতও হলো। খুৎবা ও মোনাজাতে ইমাম সাহেব পাকিস্তানের কল্যাণ কামনা করে এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুণকীর্তন করে দোয়া চাইলেন খোদার কাছে।
ইমাম সাহেব হয়তো রাজাকার ও পাকিসেনাদের দালালদের শোনানোর জন্যই অত জোরে শব্দ করে মোনাজাত জানাচ্ছেন, আল্লাহর কাছে কাঁদছেন, তাতে তার অন্তরে সায় কতখানি ছিল জানি না। তবে বাঙালি মুসল্লি কেউই যে ইমামের মোনাজাত কর্ণপাতও করেনি তা আমার দৃঢ় বিশ্বাস…”
ফিরে যাই ১৯৭১ সালের ২৭ রমজান শবে কদরের পবিত্র রাতে। ঈদের দিনতিনেক বাকি। তিন মাস আগে ১১ আগষ্ট টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরের ধলেশ্বরী নদীর উৎসমুখে মুক্তিযোদ্ধারা প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানীদের দুটি জাহাজ দখল করে প্রচুর গোলাবারুদ দখল করেছিল। ফলে ভূঞাপুর পাকিস্তানিদের বড় টার্গেটে পরিণত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা সরে যাওয়ার পর ছাব্বিশা গ্রামে ঢুকে পড়ে পাকিস্তানিরা। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এক কন্যা প্রসব করেছিলেন সাজেদা বেগম, ঠিকমত চলাফেরা করতে পারতেন না। অসুস্থ সাজেদা ঘর থেকে উঁকি দিয়ে পাকিস্তানীদের ভয়ংকর তাণ্ডবলীলা দেখে ১৫ দিনের শিশু রাবেয়া বেগমকে কোলে নিয়ে বের হয়ে পালাতে গিয়ে তাদের সামনে পড়ে যান। আল্লাহর দোহাই দিয়ে হত্যা না করার জন্য অনুরোধ করলে তাকে কোলের শিশুসহ ধাক্কা দিয়ে আগুনে ফেলে দেয় পাকিরা। মা মেয়ে দুজনেই পুড়ে জ্বলন্ত অঙ্গার হন। রোজা রেখে কোরআন শরীফ পড়ছিলেন ওমর আলী শেখের মা। মায়ের পাশে বসে শুনছিলেন ওমর আলী। হঠাৎ অতর্কিতে পাকিস্তানিরা ঢুকে পড়ে তার ছোট ভাই ইসমাইলকে মেরে ফেলে। এরপরে ওমর আলীকে গুলি করে তাকে রান্নাঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাতে নিক্ষেপ করে। এই ওমর আলীই সাজেদা বেগমের স্বামী, পুরো পরিবারটিকেই পুড়িয়ে ফেলা হয়।
অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ পরহেজগার শফিকুল ইসলাম বিলচাপড়া মাদ্রাসায় পড়ালেখা করতেন, খুব সহজ সরল অমায়িক এবং ভদ্র ছিলেন। পাকিস্তানি হানাদারদের মুখোমুখি হবার পর তিনি তাদের সালাম জানান এবং মুসলিম হয়ে তারা কেন আরেক মুসলিম ভাঈদেরকে নির্বিচারে মারছে এ প্রশ্ন করলে তাকে বেঁধে নারিকেল গাছতলায় নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। যখন পাকিস্তানি বাহিনীরা আক্রমণ করে তখন আফসার মন্ডল বারান্দায় বসে কুরআন পড়ছিলেন। পাকিদের দেখে তিনি উঠে দাড়ান, পাকিস্তানীরা তাকে গুলি করে অন্দরমহলের দিকে চলে যায়। পাকিস্তানীদের আক্রমণের পর প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন বিশা মন্ডল, সুঠাম দেহের অধিকারী খালি হাতে দু’বাহুতে দুজন সেনার গলা চেপে ধরেন, মাকে বলেন ঘর থেকে দা আনতে। দা আনতে দেরি হলে কৌশলে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে পিটিয়ে পুকুরের পানিতে নামিয়ে চুবিয়ে মারার চেষ্টা করেন। কিন্তু আরো কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা এসে বিশা মন্ডলকে পাড়ে তুলে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে, হত্যা করার পর আগুনে নিক্ষেপ করে। শবে কদরের পবিত্র দিনটায় পাকিরা রোযা রাখা মুসলমানদের উপর চালায় অমানবিক নির্যাতন, গুলি করে, আগুনে পুড়িয়ে লাশ বানায় অসংখ্য মানুষকে। সেদিন পুরো গ্রামের বাড়িঘর আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। সবুজে ভরা ছাব্বিশা গ্রামটি লাল রক্তে ভেসে যায়, জনমানবহীন আগুনে আর ধোঁয়ায় ঘেরা ভুতূড়ে গ্রামে পরিণত হয়, সেদিনের গণহত্যার তিনদিন পর ২০শে নভেম্বর ঈদের দিনে গ্রামে ঈদের নামাজ পড়ে কোলাকুলি করার মত অবশিষ্ট কোন মানুষ ছিল না।
উগ্র ধর্মান্ধ বর্বর গণহত্যাকারীরা পবিত্র রমজান মাস বা ঈদের দিন ভেবে ন্যুনতম ছাড় দেবে এটা আশা করা বোধহয় বাড়াবাড়ি। কিন্তু আসলেই থামেনি পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় রাজাকার আলবদর আলশামসদের বীভৎসতা। কিন্তু থেমে ছিল না আমাদের অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অসামান্য বীরত্বগাঁথাও। লেফট্যানেন্ট আবু মঈন মোহাম্মদ আশফাকুস সামাদ বীর উত্তম ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর ৬-এর একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। অসামান্য বীরত্বে ঈদের দিন দুর্ধষ লড়াই করে শহীদ হন তিনি, কিন্তু বিজয় এনে দিয়েছিলেন তার দলকে। লেফট্যানেন্ট আশফি ও লেফট্যানেন্ট আব্দুল্লাহর দুটো দল রায়গঞ্জের (কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার অর্ন্তগত) দখল নিতে এগিয়ে যাচ্ছিল মধ্যরাতে। অগ্রাভিযান যখন ভুরুঙ্গামারী থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে রায়গঞ্জে ‘ফুলকুমার’ নদীর ব্রিজের ওপর পৌঁছে, তখন হঠাৎ করেই তাদের পাকিস্তানিদের ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি শক্তিশালী দলের মুখোমুখি হতে হয়। পাকিস্তানীদের আচমকা গুলিবর্ষণে জিপে থাকা বিএসএফ-এর মেজর জেমস ও দুই সৈনিক নিহত হন। ২৬ নভেম্বর ১৯৭১, জয় বাংলায় প্রকাশিত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের বাণী।
২৬ নভেম্বর ১৯৭১, জয় বাংলায় প্রকাশিত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের বাণী।
 ২৬ নভেম্বর ১৯৭১, জয় বাংলায় প্রকাশিত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের বাণী।
২৬ নভেম্বর ১৯৭১, জয় বাংলায় প্রকাশিত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের বাণী।২০ নভেম্বর দিবাগত মধ্যরাতে আশফির নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা মৃত্যুমুখেও লড়ে গিয়েছিলেন অসামান্য দৃঢ়তায়! একটি মাইন বিস্ফোরণের শব্দে পাকিস্তানীরা সজাগ হয়ে গিয়েছিল, শুরু হয়েছিল আশফির দলের ওপর তীব্র মেশিনগান ফায়ার ও গোলাবর্ষণ। কতটা অকুতোভয় দুঃসাহসী কমান্ডার হলে তখন সে বলতে পারে, ‘কেউ এক ইঞ্চি পিছু হটবে না। মরলে সবাই মরব। বাঁচলে একসঙ্গেই বাঁচব।’ আমরা কি এখন এই সময়ে বসে কল্পনাও করতে পারি সেই বীরত্বটুকু?
ওদিকে সময়ের সাথে বাড়তে থাকে পাকিস্তানিদের আক্রমণের তীব্রতা, সেইসঙ্গে বাড়ে আহতদের পাল্লাও। আশফাকুস সামাদ নির্দেশ দেন তার দলকে পিছু হঠবার। কিন্তু নিজে পড়ে রইলেন সামনে, একটি বাঁশঝাড়ের আড়ালে হালকা মেশিনগান নিয়ে কাভারিং ফায়ারের লক্ষ্যে। এরই মধ্যে তিনি ওয়্যারলেসের মাধ্যমে আর্টিলারি সহযোগিতাও চান মিত্রবাহিনীর কাছে। সামাদের কাভারিং ফায়ারে তার দল নিরাপদে পিছিয়ে গেলেও তিনি পড়ে থাকেন পাকিস্তানিদের সামনে।
একের পর এক আক্রমণ আসতে থাকে তার দিকে। এভাবেই একা পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল বিক্রমে লড়ে গেলেন বিশ মিনিট। প্রচণ্ড গোলাগুলির এক পর্যায়ে হঠাৎ একটি গুলি আশফির হেলমেটের মধ্য দিয়ে ঢুকে মাথা ভেদ করে গলা দিয়ে পেটে গিয়ে নাড়িভুঁড়িতে আটকে যায়। এরপর তিনি মাটিতে পড়ে যান। মাটিতে পড়ে যাওয়ার পরেও বেঁচে ছিলেন আশফি। চিৎকার করতে থাকেন ‘পানি, পানি’ বলে। তার রানার মাহাবুব হোসেন প্রিয় স্যারের দিকে পানির একটি পাত্র নিয়ে যেতে চাইলে গুলি লাগে তার পায়েও। আশফির আর পানি পান করা হয় না। মৃত্যুর আগে এভাবেই পানি না পেয়ে স্বাধীনতার চেতনায় তৃষ্ণার্ত সামাদ পানির তৃষ্ণা নিয়েই দেশের মাটিতে ঢলে পড়েন। বেঁচে যায় তার দল। কিন্তু ইতিহাস হন সামাদ। যত সহজে তিনি বলতেন ‘খরচা’ হয়ে যাবেন, ঠিক তত সহজেই দেশের জন্য খরচ হয়ে যান তিনি। সেদিনটি ছিল ঈদের দিন। আগের রাতেই সকালের নাস্তা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মৃতদেহ উদ্ধারের সময় আশফির পকেটে পাওয়া যায় দুটো পুরি এবং এক টুকরা হালুয়া। ঈদের দিনের সকালের নাস্তা ছিল সেগুলো। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থান খুব কাছাকাছি থাকায় ওইদিন তার মৃতদেহ উদ্ধার করা যায়নি। পরে ২০ নভেম্বর দিনের বেলায় তার মৃতদেহ উদ্ধার করে ভূরুঙ্গামারীর জয়মনিরহাট মসজিদের সামনে যথাযোগ্য মর্যাদায় একই যুদ্ধে শহীদ সহযোদ্ধা সহোদর আলী হোসেন, আবুল হোসেন এবং আব্দুল আজিজকে সমাহিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে জয়মনিরহাটের নাম রাখা হয় সামাদনগর।
ওদিকে এলিফ্যান্ট রোডে জাহানারা ইমামের বাড়িতে চলছে বিশাল আয়োজন। তখনও শহরে অবরুদ্ধ বেশিরভাগ বাড়িতে তেমন কোন খাবার বা নতুন কাপড়চোপড়ের সাজসজ্জার আয়োজন সম্ভব না হলেও জাহানারা ইমাম সকালে উঠেই রান্না করেছেন ঈদের সেমাই, জর্দা। বড় ডেগচিতে তৈরী করা হয়েছে পোলাও, কোর্মা, কোপ্তা, কাবাব। তার স্বামী শরীফ ইমাম এবং ছোট ছেলে সাইফ ইমাম জামী কেউই সেসব মজাদার সুস্বাদু খাবারের এক কণাও মুখে তোলেনি। তাহলে কেন এতো রান্নার আয়োজন করলেন জাহানারা ইমাম? জানিয়েছেন তার “একাত্তরের দিনগুলি” গ্রন্থে- “...২০ নভেম্বর, শনিবার ১৯৭১। আজ ঈদ। ঈদের কোনো আয়োজন নেই আমাদের বাসায়। কারো জামা-কাপড় কেনা হয়নি। দরজা-জানালা পর্দা কাঁচা হয়নি। ঘরের ঝুল ঝাড়ু হয়নি। বসার ঘরের টেবিলে রাখা হয়নি আতরদান। শরীফ, জামী ঈদের নামাজও পড়তে যায়নি।
আমি ভোরে উঠে ঈদের সেমাই, জর্দা রেঁধেছি। যদি রুমীর সহযোদ্ধা কেউ আজ আসে এ বাড়িতে! বাবা-মা-ভাই-বোন, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন কোন গেরিলা যদি রাতের অন্ধকারে আসে এ বাড়িতে! তাদেরকে খাওয়ানোর জন্য আমি রেঁধেছি পোলাও, কোর্মা, কোপ্তা, কাবাব। তারা কেউ এলে আমি চুপিচুপি নিজের হাতে বেড়ে খাওয়াবো। তাদের জামায় লাগিয়ে দেবার জন্য এক শিশি আতরও আমি কিনে লুকিয়ে রেখেছি…। ”
মায়ের মন! আহা! বিপদসংকুল ঝুঁকি এড়িয়ে রুমীদের আসবার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। তবুও তিনি নিজ হাতে রেঁধে রেখেছেন যেন গেরিলারা ঈদের দিনটা মায়ের সাথে দেখা করতে এলে তাদের একটু ভালো খাবার খাওয়ানো যায়। রূমি বহুদিন আগে একবার জানিয়েছিল যে তাদের খাবারের অসম্ভব কষ্ট, বেঁচে থাকার জন্য যা পাচ্ছে যেভাবে পাচ্ছে বিন্দুমাত্র অভিযোগ জানাবার কথা কেউ ভাবতেও পারে না। সেজন্যই কিনা মা বাস্তবতা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে সবার আগে চিন্তা করেছেন প্রাণ হাতে নিয়ে যুদ্ধ করা সন্তানদের মুখে একটু ভালো খাবার তুলে দেবেন! অথচ এই মা মাস তিনেক আগে নিজের সন্তানকে ফিরিয়ে আনার সুযোগ পেয়েও সেটা নেননি। রুমির প্রাণভিক্ষার আবেদন করতে হত গণহত্যাকারী বর্বর ইয়াহিয়া সরকারের কাছে, কিন্তু জাহানারা-শরীফ ইমাম দম্পতি সেটা করেননি। কারণ তাতে রূমিকে অপমান করা হবে, তার জালিমের বিরুদ্ধে চিরউন্নত অকুতোভয় শির নত করা হবে।
যুদ্ধের মাঠেই ঈদ উৎসব পালনের নজিরও গড়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা, অসাম্প্রদায়িকতার এক অনুপম নিদর্শনও তৈরি হয়েছিল সেখানে। মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সচিব মাহবুব আলম ছিলেন এমনই এক ঘটনার অংশ, প্রত্যক্ষদর্শীর জবানিতে লিখেছেন বিস্তারিত- “…ঈদ মুসলমানদের জন্য প্রধান উৎসবের দিন। জন্ম থেকেই সবাই ঈদ উৎসব পালন করে এসেছে যার যেমন সঙ্গতি, সে অনুযায়ীই। ঈদের নামাজ পড়া হবে না, ঈদের উৎসব হবে না, ভালো খাওয়া-দাওয়া হবে না, ঈদের দিন সবাই হাতিয়ার হাতে শত্রুর অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে থাকবে, এরকম একটা কিছু কেউই যেন মন থেকে মেনে নিতে পারছে না। পিন্টুসহ বসে তাই সিদ্ধান্ত নিই। আর সেটা এ রকমের- ঈদের দিন নামাজ হবে, বড় খানার আয়োজন করা হবে। মোদ্দা কথা, ঈদ উৎসব পালন করা হবে যথাসাধ্য ভালোভাবেই। কিন্তু একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ছে এরকমের যে, ঈদের দিন পাকিস্তানি আর্মি ব্যাপকভাবে হামলা করবে সীমান্ত এলাকাজুড়ে। গুজবটা যেভাবেই ছড়াক, যথেষ্ট বিচলিত করে তোলে আমাদের। মুক্তিযোদ্ধারা যখন ঈদের নামাজের জন্য জামাতে দাঁড়াবে ঠিক সে সময়ই নাকি করা হবে এই হামলা।

যুদ্ধের মাঠে শত্রুবাহিনী সম্ভাব্য কোনো তৎপরতাকেই অবিশ্বাস করা যায় না। ঈদের দিন মুক্তিবাহিনীর দল যখন ঈদ উৎসবে মেতে থাকবে, দলবদ্ধভাবে নামাজ পড়তে কোথাও সমাবেত হবে, তখনি সুযোগ বুঝে পাকিস্তানিরা হামলে পড়বে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর। তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই পাকিস্তানি বাহিনীর তরফ থেকে এ ধরনের সম্ভাব্য হামলাকে সামনে রেখে আমরা ঈদুল ফিতর উৎসব উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেই।
ঈদের আগের দিন সবগুলো দল দু’ভাগে ভাগ হবে এবং সমাবেত হবে দুই জায়গায়। নালাগঞ্জ আর গোয়াবাড়িতে। ... নামাজ পড়বে একদম সীমান্তের ধার ঘেঁষে। গুয়াবাড়িতে সমবেত ছেলেরা ভারতীয় সীমান্তে উঁচু গড়ের পাদদেশে গিয়ে জামাত পড়বে। নালাগঞ্জে জামাত হবে আমগাছ তলায় পুকুরপাড়ে। মুসলমান ছেলেরা যখন ঈদের জামাতে দাঁড়াবে, তখন হিন্দু ছেলেরা কাছাকাছি অবস্থান নিয়ে হাতিয়ার নিয়ে সতর্ক পাহারায় থাকবে। হিন্দু সহযোদ্ধাদের দেওয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে মুসলমান ছেলেরা নামাজ পড়বে। এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয় গুয়াবাড়িতে একরামুলের কাছে। সোনাবানে বকর ও শামসুদ্দিনের কাছে। নালাগঞ্জে মুসা আর চৌধুরীও সেভাবেই তৈরি হয়।
হিন্দু ছেলেরা তাদের মুসলমান ভাইদের নামাজের সময় পাহারা দেবার দায়িত্ব পেয়ে যারপরনাই খুশি হয়ে উঠে। ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে এই যুদ্ধের মাঠে জীবনমরণের সবার বসবাস। এক ধর্মের মানুষ ধর্মীয় আচরণ পালন করবে, আর তাদের নিরাপদ রাখার জন্য ভিন্ন ধর্মের মানুষ হাতিয়ার হাতে পাহারা দেবে, আমার কাছে এ অভাবনীয় আর মহান মানবিক ঘটনা বলে মনে হয়। হিন্দু ছেলেদের সংখ্যা বেশি না হলেও ঈদের জামাতের সময় তাদের স্বল্পসংখ্যক সদস্য দিয়েই তারা তাদের মুসলমান ভাঈদের কীভাবে নিরাপত্তা বিধান করবে, তার পরিকল্পনায় মেতে উঠে।
... ঈদের দিনের সকাল। উৎসবমুখর পরিবেশ। সবাই আনন্দে উচ্ছল। পাশাপাশি চরম উত্তেজনা পাকিস্তান বাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণ হতে পারে। ভরতের নেতৃত্বে ৮/১০ জন হিন্দু ছেলে এগিয়ে খালের পাড়ে গিয়ে অবস্থান নেয়।
সকাল ন’টায় ঈদের জামাত শুরু হয় পুকুর পাড়ে। আমি নিজে দাঁড়াতে এবং লাঠি দিয়ে ধরে চলাফেরা করতে পারলেও নামাজ পড়তে পারি না। ওরা সবাই ঈদগাহের মত জায়গায় পবিত্র মনে নামাজে দাঁড়ায়। আমিও লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি জামাতের কাছাকাছি অবস্থানে।
যা হোক, যুদ্ধের মাঠেও আমরা তাহলে নামাজ পড়তে পারছি। গভীর এক প্রশান্তিতে ভরে উঠে মন। সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে আমি তাকিয়ে থাকি ঈদের জামাতের দিকে। না, শত্রুর হামলা হয়নি আর। পাকিস্তানিরা যেখানে সাম্প্রদায়িক ব্যাগ্রতায় রক্তপিপাসু সেখানে ঈদের জামাত আদায় করতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা রচিত করে অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের সুনিপুণ উদাহরণ…”
তথ্যসূত্র:
১। একাত্তরের দিনগুলি, জাহানারা ইমাম, সন্ধ্যানী প্রকাশনী, ঢাকা, ৪০তম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা : ২৪৪।
২। গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে, দ্বিতীয় খণ্ড, মাহবুব আলম, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ নভেম্বর ২০০৮, পৃষ্ঠা- ৩৯৮ থেকে ৩০০
৩। গৌরবের একাত্তর এবং, জেবুননেছা জেবু, প্রকাশক- বাংলার ধরিত্রী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা : ৩২।
৪। আরবান গেরিলা ফতেহ আলী চৌধুরীর সাক্ষাৎকার।
৫। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ৫ম খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, পুনর্মুদ্রন- জুন ২০০৯, পৃষ্ঠা- ২৮৮-২৮৯।
৬। মুক্তিযুদ্ধের ঈদ, সংকলন ও সম্পাদনা- আনোয়ার কবির, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা : ৬০ ৬৫।

Comments